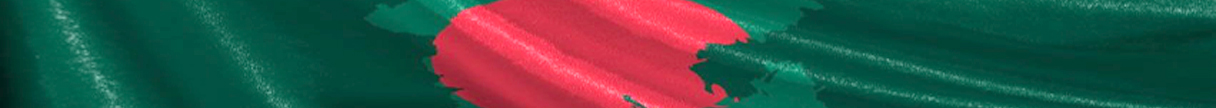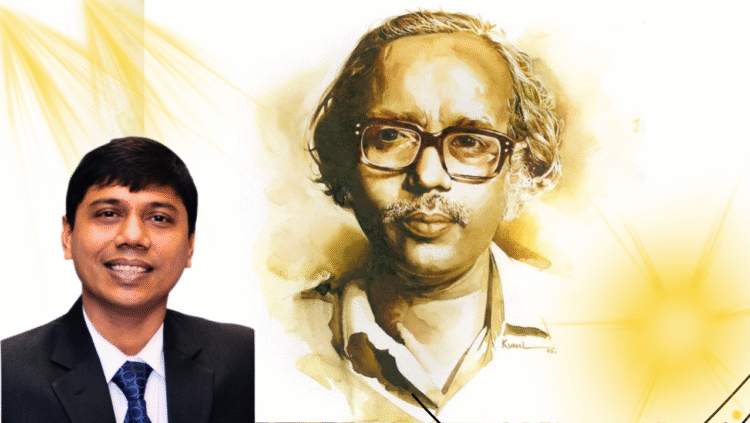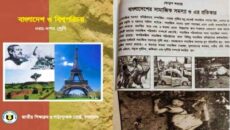বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা আধুনিক কবিতার যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-৯৫) ছিলেন সেই আগুনের এক স্বেচ্ছায় নির্বাসিত এবং দীপ্ততম স্ফুলিঙ্গ। ১৯৩৩ সালের ২৫ নভেম্বর, যে মুহূর্তে তিনি পৃথিবীতে এলেন, তা ছিল বিশ্ব ইতিহাসের এক মহাক্রান্তিকাল। একদিকে পৃথিবী ডুবে যাচ্ছিল অর্থনৈতিক মন্দার মহাবিপর্যয়ে, অন্যদিকে ভারতের মাটিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাগছিল তীব্র প্রতিরোধ। এই যুগসন্ধিক্ষণেই শোনা যাচ্ছিল ফ্যাসিবাদ ও বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি, যা পরবর্তীকালে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তিগুলো দ্রুত চুরমার করে দেয়। এই অস্থির সময়ের স্পন্দন ধারণকারী এই সংবেদনশীল মানুষটির পারিপার্শ্বিক সময়ের অস্থিরতার গভীরতম দলিল হলো তাঁর কাব্যকলা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল বেদনার এক দীর্ঘ কাহিনি। কৈশোর থেকেই তিনি অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও সমাজের কঠিন কাঠামোর প্রতি অনুভব করতেন তীব্র বিতৃষ্ণা। শৈশবেই পিতার অকালপ্রয়াণ এবং অল্প বয়সে মাতৃহারা হওয়া তাঁর জীবনে জন্ম দেয় এক গভীর নিরাপত্তাহীনতা ও শিকড়হীনতার। এই শূন্যতাই পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় গৃহহীনতার এক চিরন্তন আর্তি এবং কাব্যিক নৈরাশ্যকে তীব্রতর করে তোলে। তিনি শুধু ছন্দের কারিগর ছিলেন না; ছিলেন এক শক্তিশালী গদ্যের জাদুকর ও ভ্রমণপিপাসু ভবঘুরে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যকর্মে, বিশেষত উপন্যাস ‘কুয়োতলা’ এবং বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনিতে, এই বাউন্ডুলে জীবনের ছাপ গভীর ও স্পষ্ট। তাঁর এই বহুমাত্রিক সৃজনশীলতাই তাঁর কাব্যচেতনাকে নিরন্তর পুষ্ট করেছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী হতাশা, দেশভাগের মানসিক আঘাত এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের ধাক্কায় তাঁর ভেতরের শিল্পীসত্তার জন্ম হয়—যা ছিল একইসঙ্গে আবেগভরা এবং ভয়াবহভাবে বিদ্রোহী। শক্তির কাব্য-যাত্রা শুরু থেকেই এক উন্মুক্ত, চঞ্চল, অথচ শিল্পের প্রতি অবিচল চেতনার স্ফুরণ। তিনি যদিও ‘কৃত্তিবাস’ সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্রোহের স্রোত তাঁকে সমসাময়িক ‘হাংরি জেনারেশন’-এর বিদ্রোহের পথ থেকে সরিয়ে এক স্বতন্ত্র দার্শনিক দিগন্তে নিয়ে যায়। যদিও তিনি সামান্য কিছুকাল শিক্ষকতা বা প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করেছেন, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি সম্পূর্ণ না করা এবং স্থিতিশীল পেশায় অনীহার কারণে তাঁর জীবনে ছিল প্রচুর আর্থিক সংকট ও অনিশ্চয়তা। এই সংগ্রাম ও উন্মূল ভবঘুরে জীবনই হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার প্রধান রসদ, যা তাঁর অস্থির মনকে এক অনিবার্য শিল্পে রূপান্তরিত করে। কাজের প্রতি তাঁর এই একাগ্রতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। তাঁর বহু গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তিনি জীবনের সেরা সম্মানস্বরূপ ১৯৮৩ সালে ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’ কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এই প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান তাঁর বিদ্রোহ ও শৈল্পিক পরীক্ষাকে শেষ পর্যন্ত সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা এনে দেয়।
তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য’ (১৯৬১)-এর প্রেম কোনো সাধারণ সান্ত্বনা নয়, বরং এক দূরের, অধরা ইচ্ছাপূরণ। এই পর্বে তিনি গভীর একাকীত্বকে ভাষায় প্রকাশ করেন। যখন আমরা দেখি যে জীবনের কোনো তৈরি করা বা নির্দিষ্ট মানে নেই, সেই অর্থহীনতার সামনে দাঁড়িয়েই কবির মনে আসে সেই বিখ্যাত প্রশ্নটি। এই প্রশ্ন আজও আধুনিক মানুষের মনের দ্বিধাকে তুলে ধরে:
”যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?” (কবিতা: ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’, কাব্যগ্রন্থ: ‘ধর্মেও আছো, জিরাফেও আছো’)
এই জিজ্ঞাসা কেবল সমাজের নিয়মের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ নয়; এটি আসলে জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেয়া। জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই জেনেও, তিনি যেন নিজের ইচ্ছাতেই এক ধরণের একাকীত্ব বা ‘নির্বাসন’ বেছে নেন। যেমনটা তিনি লেখেন:
”আমি চলে যাচ্ছি / এ জন্মের মতো / সব দেনা মিটিয়ে” (কবিতা: ‘চিরন্তন’, কাব্যগ্রন্থ: ‘সোনার মাছি খুন করেছি’)
এই কথাগুলো তাঁকে ভিড়ের মধ্যেও শান্তভাবে একা থাকার সাহস জোগায়।
এই দার্শনিক হতাশা থেকেই আসে তাঁর বিদ্রোহী ভাবনা, যা ‘সোনার মাছি খুন করেছি’ (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থে আরও স্পষ্ট। এখানে ‘সোনার মাছি’ প্রতীকটি কবির ব্যক্তিগত স্বপ্ন, ভালোবাসা বা শৈশবের স্মৃতি—যাকে তিনি নিজেই ধ্বংস করেছেন। এই স্বীকারোক্তি এক গভীর আত্ম-আঘাতের চিহ্ন বহন করে। এই বিদ্রোহ শুধু বিষয়ের মধ্যে আটকে থাকেনি, তা তাঁর লেখার ধরনেও ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত সাধারণ ভাষা, লোকাল শব্দ এবং দেখতে এলোমেলো লাইনগুলো এক ধরণের ‘নিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ততা’ মেনে চলত। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ছন্দের প্রচলিত নিয়ম ভেঙে এক ছন্দপতন তৈরি করতেন। এই প্রবণতা তাঁকে ইউরোপের বিদ্রোহী কবি শার্ল বোদলেয়ারের ‘ফ্ল্যানেউর’ বা আমেরিকার চার্লস বুকোভস্কির হতাশা ও গলার স্বরের সঙ্গে তুলনীয় করে তোলে। এই নৈরাজ্য শুধু বাংলার নয়, এটি সারা পৃথিবীর আধুনিক মানুষের মনের অবস্থার অংশ।
কাব্যিক রূপক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ‘ধর্মেও আছো, জিরাফেও আছো’-এর ‘জিরাফ’ প্রতীকটি কেবল খেয়ালী নয়; এটি মধ্যবিত্ত সমাজের একাকীত্ব এবং একইসঙ্গে অবাস্তব আকাঙ্ক্ষার বা আত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। যেমন তিনি লেখেন:
”অবনি, বাড়ি আছো?” (কবিতা: ‘অবনি বাড়ি আছো’, কাব্যগ্রন্থ: ‘ধর্মেও আছো, জিরাফেও আছো’)
এই জিজ্ঞাসাটি শুধু বাড়ির খোঁজ নয়, এটি একটি স্থায়ী আশ্রয়, একটি শান্ত জীবনের প্রতি কবির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই ভিন্নধর্মী উপমাগুলো যুক্তির বাইরে গিয়ে কবির ভেতরের অনিয়ন্ত্রিত আবেগ প্রকাশ করে। এই নৈরাজ্যই বাংলা কাব্যকে এক নতুন কথা বলার স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।
তাঁর কাব্যের শেষ দিকে এসে প্রেম এবং মৃত্যুর ভাবনা এক নতুন গভীরতা পায়। তাঁর প্রেম স্পর্শযোগ্য হলেও এক অপার্থিব আকাঙ্ক্ষা—যা তাঁকে সার্ত্রের দার্শনিক দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি যেন ভালোবাসার মাধ্যমে স্বাধীনতা বা পছন্দের দায়ভারকে আরও কঠিন করে তোলেন। প্রেমিকার প্রতি তাঁর সহজ আহ্বান:
”আমি তোমাকেই ভালোবাসি—এসো” (কবিতা: ‘প্রেম’, কাব্যগ্রন্থ: ‘চতুর্দশপদী’)
এই সরলতা এক গভীর দার্শনিক আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা। মৃত্যু তাঁর কাব্যে জীবনের অনিবার্য শেষ পরিণতি হিসেবে আসে, যা নিছক নৈরাশ্য নয়, বরং জীবনের অর্থহীনতাকে মেনে নেওয়ার এক নৈরাশ্য-বিরোধী স্বীকৃতি। তাঁর এই জিজ্ঞাসা,
”মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি কি তা জানো?” (কবিতা: ‘মানুষ বড়ো কাঁদছে’, কাব্যগ্রন্থ: ‘মানুষ বড়ো কাঁদছে’)
এই করুণ প্রশ্নটি উত্তর-ঔপনিবেশিক নৈরাশ্য এবং সামাজিক যন্ত্রণা ও মৃত্যুচেতনাকে একীভূত করে দেয়, যদিও এই স্বরটি সেই সময়ের রাজনৈতিক অসন্তোষ থেকে এক সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখে, কিন্তু তা মানুষের প্রতি অস্তিত্ববাদী দায়বদ্ধতা থেকেই উৎসারিত। ‘চতুর্দশপদী’ (১৯৮২)-তে সনেটের মতো কঠিন কাঠামো ব্যবহার করে তিনি যেন এই চঞ্চল জীবনের ওপর এক ধরণের দার্শনিক শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন, যা জীবনানন্দ দাশের শান্ত প্রকৃতি বর্ণনার ধারাকে ভেঙে দিয়ে প্রকৃতিকে এক অস্থির মনের অবস্থা হিসেবে ব্যবহার করে ঐতিহ্য থেকে সরে আসা নিশ্চিত করে। তাঁর সময়ের বিখ্যাত সমালোচকরা তাঁর এই স্বরভঙ্গী ও খোলা মনকে বাংলা কবিতার এক নতুন দিগন্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের ওপর তাঁর কথা বলার স্বাধীনতা ও বিষয়ের বৈচিত্র্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাগুলো আজও খুবই দরকারি এবং প্রাসঙ্গিক থাকার কারণ হলো—তাঁর লেখায় সকল মানুষের জীবনের আসল অনুভব উঠে এসেছে। আজ যখন পৃথিবীজুড়ে প্রযুক্তি বাড়ছে এবং মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়ছে, তখন তাঁর “অবনি, বাড়ি আছো?”—এই প্রশ্নটি শুধু প্রিয়জনের খোঁজ নয়, বরং এই সময়ের একাকী মানুষটির মনে এক স্থায়ী আশ্রয় খোঁজার আকুতি। জীবনের কোনো অর্থ নেই—তাঁর এই ভাবনাটি এখনকার তরুণদের মধ্যে থাকা অস্তিত্বের ভয় বা উদ্বেগ-এর সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়, যেখানে জীবন কেন চলছে, সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। সমাজের অস্থিরতা বা বিশ্বজুড়ে চলা সংকটের মুখে তাঁর ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?’—এই কথাটি শুধু সে সময়ের নয়, এটি আধুনিক পৃথিবীর যেকোনো মানুষের মানসিক দ্বিধা এবং স্বেচ্ছায় সরে থাকার চূড়ান্ত প্রকাশ। এই গভীর সংযোগই প্রমাণ করে যে তাঁর কবিতা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লেখা হয়নি, বরং তা মানুষের বেঁচে থাকার চিরন্তন সমস্যার এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।
শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাই কেবল একজন কবি নন; তিনি এমন এক মহান শিল্পী, যিনি জীবনের গভীর কষ্টকে কবিতায় ধরে রেখেছেন। তাঁর কাব্যজীবনকে যদি আমরা এক বিশাল নদীর সঙ্গে তুলনা করি, তবে সেই নদীর শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট থেকে, কিন্তু শেষে তা মিশেছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের অনুভূতির সঙ্গে। তাঁর এই কাব্যপথের সবচেয়ে সুন্দর দিকটি হলো—তিনি জীবনের সব অনিশ্চয়তা ও বিদ্রোহ মেনে নিয়েও, এক অসাধারণ ভালোবাসা ও মানব সত্যকে প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি জানতেন, হয়তো জীবনের কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, কিন্তু পথের প্রতিটি মুহূর্তে যে জীবন আছে, সেই জীবনেই “যা আছে তাই ভালো”—এই সহজ সত্যিটাকে শিল্পে বদলে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। বিদ্রোহ ও কষ্টের মধ্যেও সুন্দর আর ভালোবাসাকে ধরে রাখার এই ক্ষমতা তাঁকে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, সারা বিশ্বের কবিদের মধ্যে এক স্থায়ী জায়গা দিয়েছে। তাঁর কবিতা ‘মানুষ বড়ো কাঁদছে’ শুধু একটি দুঃখের লাইন নয়, এটি তাঁর সব কবিতার মূল ভাবনা। এই ভাবনা একদিকে যেমন সমাজের মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ দেখায়, তেমনি অন্যদিকে পরাধীনতার পর তৈরি হওয়া ভঙ্গুর সমাজে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক অবস্থান তৈরি করে। তাঁর লেখার এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের মধ্যে কথা বলার ধরন ও বিষয়বস্তুর স্বাধীনতার বীজ বুনে দিয়ে গিয়েছে। এভাবেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর চঞ্চল জীবনকে জয় করে এক চিরস্থায়ী শিল্পে পরিণত হয়েছেন, যা আজও পাঠকের মনকে ছুঁয়ে যায় এবং তাঁর কাজের চিরায়ত গুরুত্বকে প্রমাণিত করে।
লেখক:
বাহাউদ্দিন গোলাপ
(ডেপুটি রেজিস্ট্রার, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।
Array